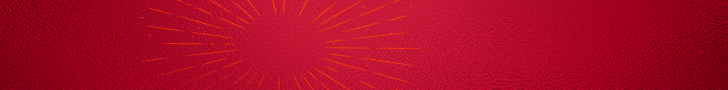বাংলাদেশে একটি জনবান্ধব সমাজ ও অর্থনীতি বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা
প্রফেসর সৈয়দ আহসানুল আলম:
বাংলাদেশ যখন উন্নয়ন ও অগ্রগতির নতুন দিগন্তে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন এক গভীর মুহূর্তের সামনে দাঁড়িয়ে
আছে — এমন একটি সমাজ গড়ার সুযোগ, যেখানে প্রতিটি নাগরিক মর্যাদা ও সমান সুযোগ পাবে।প্রফেসর
সৈয়দ আহসানুল আলম প্রণীত এই রূপরেখাটি তথ্য নির্ভর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি, যা যুব বেকারত্ব,
লিঙ্গ বৈষম্য, স্বাস্থ্যসেবার অপর্যাপ্ততা এবং শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার মতো গভীর সমস্যা মোকাবেলার জন্য
একটি সুস্পষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রদান করে।
বাংলাদেশিদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে এবং সাম্প্রতিক তথ্যেও ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা
এই নীতিমালা, ন্যায় ও অন্তর্ভুক্তির প্রতি এক সাহসী প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে। অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে
অগ্রাধিকার দিয়ে, প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করে এবং জনস্বার্থে সম্পদ পুনঃবণ্টনের মাধ্যমে, এই দলিলটি
টেকসই পরিবর্তনের একটি স্পষ্ট পথ নির্দেশ করে। এটি নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি, গবেষক ও সাধারণ
নাগরিকদেও আহ্বান জানায় — আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলি, যেখানে
প্রত্যেকে সম্মান এবং সাফল্যেও ন্যায্য সুযোগ পাবে।
১. যুবক ও নারীদের কর্মসংস্থানে ক্ষমতায়ন বাংলাদেশ বর্তমানে উচ্চ যুব বেকারত্ব এবং কম নারী শ্রম
শক্তি অংশ গ্রহণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সর্বশেষ শ্রম শক্তি জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ১৯.৪ লাখ যুবক (১৫
২৯বছর বয়সীদেও ৭.২%) বেকার (১) জাতীয় বেকারত্বেও হার প্রায়৩.৫%, কিন্তু যুবাদেও ক্ষেত্রে তা
দ্বিগুণেরও বেশি (৮%) (২) এদিকে, নারী শ্রম শক্তি অংশগ্রহণ মাত্র -৩৭% (২০২৩), যেখানে পুরুষের
অংশগ্রহণ প্রায়-৮০% (৩) আরও উদ্বেগজনক হলো, ১৫-২৪বছর বয়সী তরুণী মেয়েদেও মধ্যে ৬২%
ঘঊঊঞ (শিক্ষা, কর্মসংস্থান অথবা প্রশিক্ষণের বাইরে) অবস্থায় আছে(৪) এই পরিসংখ্যানগুলিই প্রমাণ করে
কেন যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান এবং নারীদেও কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো জরুরি।
দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ, নারীদের জন্য কর্মসংস্থান প্রণোদনা এবং উদ্যোক্তা সহায়তা বৃদ্ধি করে এই
নীতিমালা তরুণ এবং নারীদের উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত করতে চায়, যা সরাসরি বিদ্যমান ঘাটতিগুলো
মোকাবেলা করবে।
২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি যদিও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় $২,৭৮৪ -এ পৌঁছেছে (৫), কিন্তু এই সমৃদ্ধি সবার মধ্যে সমানভাবে বিতরণ হয়নি। জাতীয় গড়ে মাসিক পারিবারিক
আয় ৩২,৪২২টাকা হলেও, গ্রামে তা মাত্র ২৬,১৬৩টাকা, আর শহরে ৪৫,৭৫৭টাকা (৬)। এতে গ্রাম-শহর
আয়ের বৈষম্য স্পষ্ট। ২০২২ সালের তথ্যে দেখা যায়, এখনো ১৮.৭% জনগণ দারিদ্রের মধ্যে বাস করে —
গ্রামে ২০.৫% এবং শহরে ১৪.৭% (৭)। বিশেষ করে বরিশাল বিভাগের দারিদ্রের হার সর্বোচ্চ-
(২৬.৯%)(৮)। এই বৈষম্যই নীতিমালার "অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি"র অগ্রাধিকারে যুক্তি দেয়।
গ্রামীণ উন্নয়ন, জীবিকা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্কে বিনিয়োগ করে প্রস্তাবিত নীতিমালা প্রান্তিক
জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করে।
বিশেষ করে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গ্রামাঞ্চলে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করলে বর্তমান
আয়ের বৈষম্য কমবে এবং প্রবৃদ্ধি আরও ন্যায্য হবে।
৩. স্বাস্থ্য সেবার প্রবেশ গম্যতা উন্নয়ন (গ্রাম-শহর ভারসাম্য) বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা অত্যন্ত
অসম।
দেশের ৬৬%-এর বেশি মানুষ গ্রামে বাস করে, যেখানে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া এখনও বড় চ্যালেঞ্জ (৯)।
গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালও চিকিৎসকের ঘাটতির কারণে স্বাস্থ্যগত ফলাফল খারাপ হচ্ছে। যেমন, গ্রামাঞ্চলে
মাত্র ৪২.৮% মায়ের চারটি প্রসব পূর্ব সেবা নেওয়া হয়, যেখানে শহরে তা ৫৯% (১০)।
গ্রামে মাত্র ৪৫% জন্ম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হয়, শহরে তা ৬৩% (১১)। বাংলাদেশে প্রতি ১,০০০জনে মাত্র- ০.৬৭জন
চিকিৎসক রয়েছে, এবং তাদের বেশিরভাগ শহরে কেন্দ্রীভূত (১২) (১৩)। নার্সের সংখ্যা আরও কম, প্রতি
১,০০০জনে মাত্র ০.৬১জন (১৪)। হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (ইঐঋঝ) ২০২২ অনুযায়ী, দেশে মোট
১৩,৯০৭টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে, যার মধ্যে শহরে ২৪.৩% এবং গ্রামে ৭৫.৭% (১৫)। সরকারি
প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধান (৭১.৬%), কিন্তু শহরে ব্যক্তিগত হাসপাতালের সংখ্যা অনেক বেশি (৪৫.৬% বনাম
গ্রামে ১৯.৭%)। এই তথ্যগুলো স্বাস্থ্যসেবায় অবকাঠামো ও পরিষেবার প্রবেশ গম্যতায় নগর-গ্রাম বৈষম্যের
ইঙ্গিত দেয়।
সুতরাং, গ্রামাঞ্চলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উন্নয়ন, গ্রামে চিকিৎসক ও ইন্টার্ন পাঠানো এবং গ্রামীণ
পরীক্ষাগার আধুনিকায়ন এই নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ। এগুলো বাস্তবায়ন করলে স্বাস্থ্যসেবার ন্যায্য
প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হবে, যেমনটি এই রূপরেখায় কল্পনা করা হয়েছে।
৪. নার্সিং ও চিকিৎসা প্রশিক্ষণ জোরদার করণ বাংলাদেশে প্রশিক্ষিত নার্সের সংকট স্বাস্থ্যসেবার মানকে
মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত নার্সের সংখ্যা প্রায় ১,৬৮,৬৩০জন (১৬)।
নার্স-চিকিৎসক অনুপাত ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ১.৬:১, যা ২০১৩সালের ০.৪:১অনুপাত থেকে উন্নতি
হলেও এখনো বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার (ডঐঙ) সুপারিশকৃত ৩:১ মানদণ্ডের অনেক নিচে। শহরাঞ্চলের
হাসপাতালে তুলনামূলক ভালো অবস্থা দেখা গেলেও গ্রামাঞ্চলে মারাত্মক নার্স সংকট রয়েছে, যেখানে
অনভিজ্ঞ স্বাস্থ্য কর্মীদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এই দীর্ঘ স্থায়ী ঘাটতি স্বাস্থ্যসেবার মান ক্ষুণ্ন করে,
নার্সদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং স্বাস্থ্যকর্মী বিতরণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্যকে প্রতিফলিত করে
(১৫)।
এই সমস্যার সমাধানে, প্রস্তাবনাগুলো নার্সিং শিক্ষা সম্প্রসারণের আহ্বান জানায়।
বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৬১টি নার্সিং ইন্সটিটিউট (সরকারি-৭০, স্বায়ত্তশাসিত-৮, বেসরকারি-৩৮৩টি) রয়েছে
(১৭)। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট ও স্বল্প আসন সংখ্যার কারণে অনেক আসন খালি থাকে, এবং
বর্তমান নার্স উৎপাদন প্রয়োজনের মাত্র - ২৪% মেটাতে সক্ষম(১৮)। নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন ও ভর্তি
সংখ্যা বাড়িয়ে এই নীতিমালা স্বাস্থ্য খাতে প্রশিক্ষিত কর্মী বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়,
২০২২ সালে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ১৫% নারী ছিল (২১,৮৮১
জন) (১৯)।
এ কারণে নার্সিং ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো অপরিহার্য।
নার্সিং কলেজে বিনিয়োগ এবং নার্সিং পেশার জন্য প্রণোদনা বাড়ানো হলে স্বাস্থ্যখাতের কর্মী বাহিনী শক্তিশালী
হবে — যা তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান ঘাটতির সরাসরি প্রতিক্রিয়া।
৫. খাদ্য নিরাপত্তা ও ভোক্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করণ বাংলাদেশে খাদ্যনিরাপত্তা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।
প্রতি বছর আনুমানিক ৩ কোটি মানুষ খাদ্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয় (২০), যা দূষিত বা ভেজাল খাদ্য গ্রহণের
কারণে ঘটে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্ত ৃপক্ষ (ইঋঝঅ) এর পরীক্ষায় দেখা গেছে, এক বছরে ৮,৩৯১টি
খাদ্য নমুনার মধ্যে ৭৪৫টি পণ্যে ভেজাল পাওয়া গেছে (৯%) (২১)। ২০১৫-২০১৯ সাল পর্যন্ত, বিএফএস
এ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৫,৭৪৩টি অভিযান পরিচালনা করে ১০,০০০এরও বেশি অপরাধীকে দণ্ডিত
করেছে এবং ৮৮লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে (২১)। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাস্তবায়ন এখনো
দুর্বল এবং বিএফএস এ পর্যাপ্ত জনবল সংকটে ভুগছে। প্রস্তাবনাগুলো এই সমস্যা সমাধানে বিএফএসএ-র
সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে — যেমন অধিকতর পরিদর্শক নিয়োগ, পরীক্ষাগার উন্নয়ন, এবং কঠোর
শাস্তি প্রবর্তন।
এছাড়া আন্তঃসংস্থাগত সমন্বয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে (২১)।
এই পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করলে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত
করা সম্ভব হবে।
৬. ন্যায় বিচারের প্রসার:
বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ বাংলাদেশে বিচার প্রাপ্তি প্রায়ই দেরি হয় এবং রাজধানী কেন্দ্রীভূত, যা বিচার
বিভাগে বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্ব তুলে ধরে।
২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দেশে মোট ৪.৫১মিলিয়ন মামলা বিচারাধীন ছিল, যা আগের বছরের ৪.২৯মিলিয়ন
থেকে বেড়েছে (২২)।
নিম্ন আদালতেই প্রায় ৩.৯মিলিয়ন মামলা পরিচালিত হয়।
দেশজুড়ে মাত্র ২,০০০ সক্রিয় বিচারক রয়েছেন, অর্থাৎ গড়ে প্রতি ৮৫,০০০জনের জন্য মাত্র ১জন
বিচারক(২২)।
উচ্চ আদালতের সব বেঞ্চ ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভূত, ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উচ্চ আদালতের সেবা
নিতে হলে ঢাকায় আসতে হয়।
এই অবস্থার পরিবর্তনে, সংস্কার কমিশন প্রতিটি বিভাগীয় শহরে স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপনের সুপারিশ
করেছে(২৩), সাথে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে আদালত সম্প্রসারণের প্রস্তাব দিয়েছে।
এতে চট্টগ্রাম বা রাজশাহীর মতো অঞ্চলের মানুষ ঢাকায় না গিয়েই স্থানীয় হাইকোর্টবেঞ্চ থেকে আপিল
করতে পারবে।
বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ, নতুন বিচারক নিয়োগ এবং নতুন আদালত স্থাপনের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির
গতি বাড়বে।
এছাড়া, স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় আইনি সহায়তা কর্মসূচি (ঘধঃরড়হধষ খবমধষ অরফ) ও মধ্যস্থতা সেবা
সম্প্রসারণের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (২৩)।
এই পদক্ষেপগুলি দ্রুত, সুলভ ও ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করবে — যা তথ্য-ভিত্তিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৭. অপরাধ দমন ও দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণ সাম্প্রতিক অপরাধ পরিসংখ্যান বাংলাদেশে
উদ্বেগজনক বাস্তবতা প্রকাশ করে।
২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত, ২২৪জন মেয়ে শিশুধর্ষণের শিকার হয়েছে, ৮১জন নিহত
হয়েছে এবং ১৩৩জন আত্মহত্যা করেছে (২৪)।
গত ১০বছরে (২০১৪-২০২৪) ১৮বছরের নিচের ৫,৬৩২মেয়ে শিশু ধর্ষণের মামলা রেকর্ড হয়েছে (২৫)।
২০২৩সালে পুলিশের তথ্য অনুযায়ী ৫,১৯১টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে, ২০২৪সালে ৪,৩৯৪টি মামলা
হয়েছে। ২০২৩ জানুয়ারি থেকে ২০২৫ জানুয়ারির মধ্যে মোট ৯,৯৭৭টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে, যা গড়ে
প্রতিদিন ১৩জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হওয়ার চিত্র তুলে ধরে (২৫)। কিন্তু দুর্ভাগ্য জনকভাবে, এই
মামলাগুলোর মাত্র ৩% দোষী সাব্যস্ত হয় (২৬)(২৭)(২৮)। ব্র ্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় দেখা গেছে,
২০০৯-২০১৪সালের মধ্যে তিনটি ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের মামলায়
দণ্ডের হার মাত্র ০.৮৬% ছিল (২৯)।এই বিচারহীনতার সংস্কৃতি সহিংসতা আরও বাড়িয়ে দেয়।
জনগণের নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, নীতিমালায় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন, সাক্ষী সুরক্ষা
শক্তিশালীকরণ এবং দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ছোট খাটো অপরাধে মোবাইলকোর্টের
ব্যবহার বাড়িয়ে মামলার জট কমানো এবং তাৎক্ষণিক প্রতিকার নিশ্চিত করার প্রস্তাব রয়েছে। তবে এটি
যেন যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া বজায় রেখে পরিচালিত হয়, তা নিশ্চিত করার দিকেও বিশেষ নজর দেয়া
হয়েছে।
এই পদক্ষেপগুলো কার্যকর করলে "বিচার বিলম্বিত মানেই বিচার অস্বীকার" সমস্যার সমাধান হবে এবং
জনগণের মধ্যে বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা বাড়বে।
৮. জনগণের চাহিদার প্রতি বাজেট অগ্রাধিকার পুন:র্নির্দেশ
বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে জনসম্পদ ব্যবহারে সামাজিক উন্নয়নখাত অবহেলিত থেকেছে। বাজেট বরাদ্দ নিয়ে
নাগরিক অসন্তোষ ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে মোট দেশজ
উৎপাদনের (এউচ) তুলনায় বরাদ্দ খুবই কম রয়েছে — যেমন, ২০২৩সালে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়
এউচ-র মাত্র-০.৭% এবংশিক্ষাখাতে-১.৬% (৩০)। ফলে পরিবারের ওপর ব্যয়ের ভার চাপছে: স্বাস্থ্য খাতে
৭২% ব্যয় পরিবারগুলোকেই বহন করতে হয় — যা বৈশ্বিকভাবে সর্বোচ্চহারগুলোর একটি। একইভাবে,
শিক্ষা খরচেরও প্রায় ৭১% পরিবারগুলো বহন করে। অন্যদিকে, বড় অবকাঠামো প্রকল্পে বরাদ্দ উদারভাবে
দেয়া হচ্ছে।
এই প্রস্তাবনাগুলো জনগণের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট অগ্রাধিকার পুনর্গঠনের আহ্বান জানায়।
স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে এউচ-র ৫-৬% পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ করা (যেমন সমপর্যায়ের দেশগুলো করে)
বহুদিনের অবহেলিত খাতের উন্নতি সাধন করবে। সরকারের নিজস্ব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও স্বাস্থ্যখাতে
উন্নয়ন বাজেটের ১১% এবং শিক্ষাখাতে ১৬.৫% বরাদ্দের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা বাস্তবে পূরণ
হয়নি। বাজেটে মানব উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে — যেমন স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ <১% থেকে বাড়িয়ে
সুপারিশকৃত ৩%-এ পৌঁছানো — হাসপাতাল, স্কুল ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।
জনমত ও পরিষ্কারভাবে এই পরিবর্তনের পক্ষে, কারণ মানুষ চায় এমন খাতে ব্যয় বাড়ুক, যা তাদের জীবন
সরাসরি উন্নত করে (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, কর্মসংস্থান), শুধু বিশাল মেগা প্রকল্পের পরিবর্তে (৩০)।
এই বাজেট সংস্কার ও স্বচ্ছতার উদ্যোগে নিশ্চিত হবে যে, সম্পদ ন্যায্যভাবে সর্বাধিক প্রভাব ফেলে এমন
ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হবে।
৯. নারী, যুবক এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তিসম্প্রসারণ
বাংলাদেশের একটি বড় অংশ এখনো আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবার বাইরে রয়েছে, বিশেষ করে নারী, তরুণ
এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। ২০২১সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদের মাত্র ৫৩% কোনো ব্যাংক বা মোবাইল
মানি সেবা দাতা প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাউন্ট খুলেছে (৩১)(৩২)। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক জনগণ এখনো ব্যাংকিং ব্যবস্থার
বাইরে।
নারী-পুরুষের মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ফাঁরাক এখনো লক্ষণীয় — নারীদের অ্যাকাউন্ট মালিকানা পুরুষদের
তুলনায় ১৯শতাংশ পয়েন্ট কম (৩৩)। (২০১৭সালে এই ব্যবধান ছিল ২৯%।) গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগণ ও
নগদ অর্থ বা অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থারও পরনির্ভরশীল। এ কারণেই প্রস্তাবনাগুলো ব্যাংকিং অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর
সুপারিশ করছে।
সহজ অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া, গ্রামে এজেন্ট ব্যাংকিং সম্প্রসারণ এবং লক্ষ্য ভিত্তিক আর্থিক পণ্য প্রবর্তনের
মাধ্যমে আরও বেশি জনগণকে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে —
২০২২সালে প্রায় ১৪.১% পরিবার নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছে, যা ২০১৬সালের তুলনায় দ্বিগুণ(৩৪)।
বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নারী ও তরুণদের ওপর: মোবাইল ব্যাংকিং ও ডিজিটাল ফাইন্যান্সের প্রসার
তাদের চলাচল ও সাক্ষর তার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সাহায্য করছে। মোবাইল মানি সেবা বৃদ্ধির ফলে
নারী-পুরুষের ফাঁরাক ২৯% থেকে ১৯%-এ নেমেছে (৩৩)। আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং তরুণ-বান্ধব
ব্যাংকিং (যেমন ছাত্র অ্যাকাউন্ট) চালু করে এই অন্তর্ভুক্তি আরও বাড়ানো সম্ভব।
নারী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ, সঞ্চয় ও লেনদেনের সুযোগ তৈরি করে এই নীতিমালা সামগ্রিকভাবে
ন্যায্য প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।
১০. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, নারী ও স্টার্ট আপের জন্য ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (ঝগঊ) বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলেও, অর্থায়ন পেতে প্রায়ই নানা
বাধার সম্মুখীন হয়। তথ্য অনুযায়ী, এমএসএমই (গঝগঊ) খাতে বর্তমানে ২.৮বিলিয়ন ডলারের আর্থিক
ঘাটতি রয়েছে এবং নারী পরিচালিত ঝগঊ-এর ৬০% ঋণ চাহিদা অপূর্ণ (৩৫)। নারীরা এখন দেশের মোট
ব্যবসার প্রায় ১০-১২% পরিচালনা করছে (২০১৩সালের ৭.২%-এর তুলনায় উন্নতি হলেও), তবে তারা
ব্যাংক ঋণের খুব সামান্য অংশ পাচ্ছে। উচ্চ জামানত চাহিদা ও পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে নারী
উদ্যোক্তা এবং তরুণ স্টার্ট আপরা প্রায়ই ঋণ প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হয়। এই প্রস্তাবনাগুলো ঋণ কাঠামোসহজীকরণ
এবং এই গোষ্ঠীগুলোর জন্য বিশেষ ঋণ সহায়তার আহ্বান জানায়। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে কিছু
পদক্ষেপ নিয়েছে — যেমন, ২০২৩সালে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদের (৫%) রিফাইন্যান্স স্কিম চালু
করেছে এবং ব্যাংকগুলোকে নারী উদ্যোক্তাদের কাছে ঋণ দিতে উৎসাহিত করেছে (৩৫)।
এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, প্রস্তাবনাগুলো নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ঋণ সংস্থান, নারীদের জন্য
জামানতমুক্ত বা গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ প্রদান এবং গ্রামীণ ঝগঊ-এর জন্য সহজ ঋণ প্রক্রিয়া চালুর সুপারিশ
করে। বর্তমানে ঝগঊ-র প্রায় ৪৬% ঋণ পেতে সক্ষম হয়েছে (৩৫), অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি এখনো বঞ্চিত।
ব্যাংকগুলোর জন্য ঝগঊ খাতে (বিশেষ করে ঢাকা-চট্টগ্রামের বাইরে) আরও বেশি ঋণ বিতরণের
বাধ্যবাধকতা আরোপ এবং তরুণ উদ্ভাবকদের জন্য কোটা নির্ধারণের মাধ্যমে ছোট ব্যবসার বিকাশ ত্বরান্বিত
করা হবে।
বিশেষভাবে নারী উদ্যোক্তারা, যারা এক বিশাল সম্ভাবনাময় জনশক্তি, এতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে।
সংক্ষেপে, সরকার-বেসরকারি তহবিল, স্বল্প সুদের স্কিম এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধার মাধ্যমে ঝগঊ
ওস্টার্ট আপের জন্য ঋণ প্রাপ্তির পথ সহজ করে এই নীতিমালা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ন্যায়ভিত্তিক
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শক্তিশালী করবে।
১১. কৃষিশিল্প এবং গ্রামীণ ঋণ সহায়তা
বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৪৫% কৃষিতে নিয়োজিত এবং কৃষিখাত দেশের এউচ-র ১১% অবদান
রাখে, তবুও কৃষক এবং কৃষিশিল্পগুলো আনুষ্ঠানিক ঋণের খুব অল্প অংশ পেয়ে থাকে (৩৬)। ২০২৩ অর্থবছরে
ব্যাংকসমূহ প্রায় ৩২৮বিলিয়ন টাকা কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ বিতরণ করেছে (৩৬), যা লক্ষ্য পূরণ করেছে — কিন্তু
এটি মোট ব্যাংক ঋণের মাত্র ২.৫-৩%। আসলেই, বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের ঋণ পোর্টফোলিওর ২%
এরও কম কৃষি খাতে বিনিয়োগ করে (৩৭)। (বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যূনতম ২% কৃষি ঋণ বরাদ্দের নির্দেশনা
দিয়েছে)।
গ্রামীণ পরিবারের বেশিরভাগই মাইক্রো ফাইন্যান্স এনজিও বা অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতার ওপর নির্ভর করে;
কৃষক পরিবারের মধ্যে যারা ঋণ নিয়েছে, তাদের ৬৩% এনজিও থেকে এবং মাত্র ২৬% ব্যাংক থেকে ঋণ
নিয়েছে (৩৬)।
এছাড়া, ব্যাংকগুলো সাধারণত ক্ষুদ্র কৃষকের পরিবর্তে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীকে ঋণ
দিতে বেশি আগ্রহী।
এই ঘাটতি দূর করতে, প্রস্তাবনাগুলো কৃষিখাত এবং কৃষি শিল্পের জন্য ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর আহ্বান জানায়।
বিশেষত, কৃষি ঝগঊ (যেমন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কোল্ড স্টোরেজ, কৃষি যন্ত্রপাতি সেবা) এর জন্য
রিফাইন্যান্স স্কিম জোরদার করা এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ক্ষমতা বাড়ানোর
সুপারিশ করা হয়েছে।
কৃষি শিল্পের ঋণে সুদ ভর্ত ুকি বা ক্রেডিট গ্যারান্টি চালু করলে ব্যাংকগুলোকে কৃষিখাতে আরও বেশি ঋণ
প্রদান করতে উৎসাহিত করা যাবে। গ্রামাঞ্চলে শাখাবিহীন ব্যাংকিং এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্স সেবা
সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছে ঋণ পৌঁছানোর ব্যবস্থাও প্রস্তাবিত হয়েছে। কৃষি শিল্পের
উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করলে শুধু গ্রামীণ আয় বাড়বেনা, বরং ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমবে
এবং কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজনও হবে।
এই পদক্ষেপগুলো কৃষিখাতের অর্থনৈতিক গুরুত্বের তুলনায় চলমান অর্থায়ন ঘাটতি দূর করতে এবং গ্রামীণ
ন্যায়বিচার ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়ক হবে।
১২. নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য আবাসন ও শহুরে বস্তির সমস্যা মোকাবিলা
বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের ফলে নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য আবাসন সংকট আরও তীব্র হয়েছে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ইইঝ)-এর ২০২৪সালের হালনাগাদ তথ্যে দেখা গেছে, বর্তমানে দেশে প্রায়
৩.৫মিলিয়ন মানুষ বস্তিতে বাস করছে — যা ২০১৪সালের ২.২৩মিলিয়নের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।
এর মধ্যে ঢাকায়ই রয়েছে প্রায়২.৮মিলিয়ন বস্তিবাসী, যাদেশের মোট বস্তিবাসীর ৮০%।
৭৮% বস্তির পরিবার একক কক্ষে বসবাস করে — যা চরম জনাকীর্ণতার ইঙ্গিত দেয়। পাইপলাইনের পানির
সুবিধা রয়েছে মাত্র ৩৫% পরিবারের এবং ৪২% পরিবারের যথাযথ স্যানিটেশন সুবিধা নেই। গ্রাম-শহর
অভিবাসন এবং জমির মূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০১৪সালের পর থেকে অনানুষ্ঠানিক বসতির সংখ্যা ২২% বৃদ্ধি
পেয়েছে।
এই চিত্র স্পষ্টভাবে দেখায় যে, বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিত করতে
জরুরি নীতিগত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, বিশেষ করে ঢাকায়, যেখানে ৯২% নতুন অভিবাসী অনানুষ্ঠানিক
বসতিতে আশ্রয় নেয় (৩৮)। এই নীতিমালার মাধ্যমে সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প সম্প্রসারণ, বস্তি উন্নয়ন এবং
দরিদ্র জনগণের জন্য আবাসন ঋণ সহজীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ভর্ত ুকি যুক্ত
অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ বা বিদ্যমান বস্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন (পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ সংযোগ) করলে
সরাসরি লাখ লাখ শহুরে দরিদ্র উপকৃত হবে, যারা এখন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উচ্চ ভাড়ায় বসবাস করে।
এই প্রস্তাবনা বড় মাপের নিম্ন আয়ের গৃহায়ন ঘাটতি দূর করতে সহায়ক হবে।
এছাড়া, নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য আবাসন তহবিল বা মাইক্রো-মর্টগেজ স্কিম চালুর সুপারিশ করা
হয়েছে, যাতে কেবল ধনী শ্রেণি নয়, দরিদ্ররাও গৃহস্বত্ব অর্জন করতে পারে। আবাসনের সাথে স্বাস্থ্য ও
নিরাপত্তা সরাসরিযুক্ত; উন্নত আবাসন ব্যবস্থাপনা বস্তিতে রোগ ব্যাধি ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমাবে। মোটকথা,
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং কমিউনিটি নেতৃত্বাধীন আবাসন উদ্যোগের মাধ্যমে "সবার জন্য
আবাসন" নীতির বাস্তবায়ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সামাজিক মর্যাদায় পরিণত করতে সহায়ক
হবে।